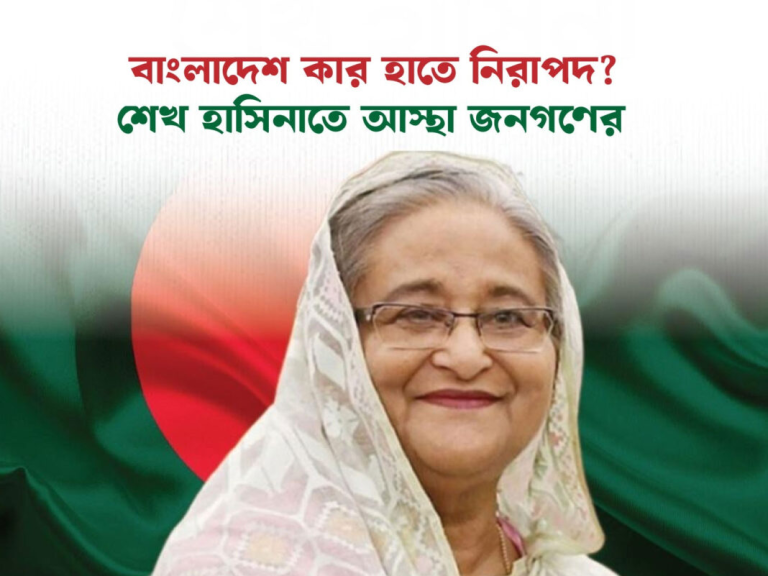সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ছবি আসলে এডিটেড। আসল ছবিটি ছিল পানামার প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডির সাথে তোলা। ভুয়া ছবির এই কেলেঙ্কারি ডিজিটাল যুগে তথ্য যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তাকে নতুন করে সামনে আনলো।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ছবি মুহূর্তেই আলোড়ন তুলেছিল— মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তার স্ত্রী মেলানিয়া ট্রাম্পের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও তার কন্যা। ক্যাপশন ঘিরে আরও কৌতূহল: “US President Donald Trump and First Lady Melania Trump pose for a picture with Bangladesh Chief Adviser Professor Muhammad Yunus and his daughter Deena Yunus during a reception hosted by the US President on September 23 in New York.”
প্রথমে অনেকে ভেবেছিলেন এটি জাতিসংঘ অধিবেশনের ফাঁকে আয়োজিত আনুষ্ঠানিক ছবির মুহূর্ত।
কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সত্য উন্মোচিত হয়—ছবিটি আসল নয়, বরং অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ডিজিটাল এডিটিংয়ের মাধ্যমে তৈরি।
অনুসন্ধানে দেখা যায়, ছবির আসল সংস্করণে ড. ইউনূস ছিলেন না।
সেখানে ছিলেন পানামার প্রেসিডেন্ট হোসে রাউল মুলিনো ও তার স্ত্রী ফার্স্ট লেডি মারিসেল কোহেন দে মুলিনো।
নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনের সময় আয়োজিত এক সংবর্ধনায় তাঁরা ট্রাম্প দম্পতির সঙ্গে সেই ছবি তুলেছিলেন।
পানামার একাধিক সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারকারীরা ইতিমধ্যেই ছবিটি প্রকাশ করেছিলেন।
অর্থাৎ, ভাইরাল হওয়া ছবিটি মূল ফ্রেম থেকে পানামার প্রেসিডেন্ট ও ফার্স্ট লেডিকে বাদ দিয়ে তাদের স্থলে ড. ইউনূস ও তার মেয়েকে বসানো হয়েছে।
দুটি ছবি পাশাপাশি রাখলে পার্থক্য একেবারেই পরিষ্কার হয়ে যায়—
ট্রাম্প দম্পতির পোশাক ও অবস্থান—দুটো ছবিতেই অভিন্ন।
পটভূমি ও মার্কিন পতাকার অবস্থান—সম্পূর্ণ একই।
আলো ও ছায়ার বিন্যাস—হুবহু এক, যা প্রমাণ করে মূল ছবির উপরেই কারসাজি হয়েছে।
অতএব, এই ঘটনা নিছক গুজব নয় বরং একটি সচেতন ডিজিটাল ম্যানিপুলেশন।
প্রশ্ন উঠছে—
কারা এবং কেন এই ধরনের ভুয়া ছবি প্রচার করছে?
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ড. ইউনূসকে আরও প্রভাবশালী হিসেবে উপস্থাপন করা।
অনেকে যাচাই না করে শেয়ার করেন, ফলে তথ্যের বিকৃতি ছড়ায়।
ডিজিটাল যুগে ছবির শক্তি এতটাই প্রবল যে, একটি ছবি পুরো ন্যারেটিভ বদলে দিতে পারে।
এই ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তীব্র সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেকেই বলেছেন, ভুয়া ছবি শেয়ার করা শুধু ব্যক্তির ভাবমূর্তিই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং দেশেরও কূটনৈতিক সম্পর্কের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন, ডিজিটাল ম্যানিপুলেশন এখন এক ধরনের রাজনৈতিক অস্ত্র, যার শিকার হতে পারে যে কোনো দেশ ও ব্যক্তি।
এই ঘটনা আবারও প্রমাণ করলো—
ডিজিটাল যুগে চোখে দেখা প্রতিটি ছবিই সত্য নয়।
একটি ছবি বা সংবাদ শেয়ার করার আগে ফ্যাক্ট-চেক করা জরুরি।
ভুয়া তথ্য ও ছবির প্রচার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের ভাবমূর্তির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারে।
ড. ইউনূস–ট্রাম্প ছবি বিতর্ক আসলে আমাদের সামনে এক বড় সতর্কবার্তা রেখে গেছে: প্রযুক্তি যতই উন্নত হোক, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা ছাড়া তথ্যের সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব নয়।