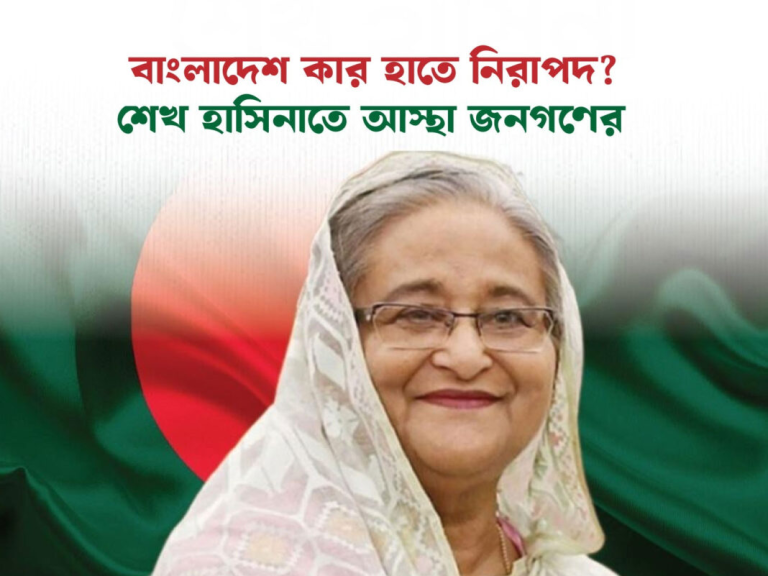ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ৩১ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীর মৃত্যু ঘটেছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন, নির্যাতন ও পরিকল্পিত হত্যার অভিযোগে দেশজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।
ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময়ে একের পর এক আওয়ামী লীগ নেতা, কর্মী ও সমর্থকের মৃত্যু এখন দেশের রাজনৈতিক পরিসরে এক গভীর আতঙ্কের নাম। সর্বশেষ প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, ৩১ জন রাজনৈতিক বন্দি বিচারবিভাগীয় হেফাজতে মারা গেছেন—যাদের অধিকাংশই ক্ষমতাচ্যুত দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।
এই ঘটনাগুলো কেবল একটি সরকারের মানবাধিকার চর্চার মানদণ্ড নয়, বরং রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থার নৈতিক দায়বদ্ধতাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করছে।
এই ৩১টি মৃত্যুর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই “হৃদরোগ” বা “অসুস্থতা”কে সরকারি কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
কিন্তু নিহতদের পরিবার ও রাজনৈতিক সহকর্মীদের দাবি, এসব মৃত্যুর পেছনে ছিল গোপন নির্যাতন ও পদ্ধতিগত দমননীতি।
বিশেষত খুলনা মহানগর যুবলীগ নেতা জয়নাল আবেদিন জনি-এর মৃত্যুতে “পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে—যা এ ঘটনার ভয়াবহতা বাড়িয়েছে।
একইভাবে গোপালগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা ও নওগাঁ অঞ্চলে মৃত নেতা-কর্মীদের অধিকাংশের পরিবার নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে।
এমনকি সাবেক মন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনও চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন—যা নিয়েও ওঠে নির্যাতনের অভিযোগ।
মানবাধিকার সংস্থা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে,
বিচারবিভাগীয় হেফাজতে ধারাবাহিক রাজনৈতিক মৃত্যুর এই ঘটনাগুলো বাংলাদেশের আইনি কাঠামো ও ন্যায়বিচারের প্রতি বিশ্বাসকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ করছে।
তারা প্রশ্ন তুলেছেন —
“যদি আদালতের তত্ত্বাবধানে থাকা নাগরিক নিরাপদ না থাকেন, তবে সাধারণ নাগরিক কোথায় নিরাপত্তা খুঁজবে?”
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলো এরইমধ্যে নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।
কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়নি—যা সরকারের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার প্রশ্নকে আরও তীব্র করেছে।
রাজনৈতিক বন্দিত্ব ও রাষ্ট্রীয় প্রতিশোধের রাজনীতি
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বন্দিত্ব ও ‘কারাগারে মৃত্যু’ নতুন কিছু নয়।
তবে এই সময়কার ঘটনাগুলো একেবারে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে কারণ এগুলো ঘটছে বিচারবিভাগীয় হেফাজতের মধ্যেই—অর্থাৎ আদালতের আওতায় থাকা নাগরিকদের মৃত্যু ঘটছে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন,
এটি একধরনের ‘বিচারিক প্রতিশোধ’ বা ‘institutional repression’, যেখানে রাষ্ট্র তার বিরোধীদের শাস্তি দিতে বিচারব্যবস্থাকেও ব্যবহার করছে।
জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল (UNHRC), অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতো সংস্থাগুলো এই ঘটনাগুলো নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
তারা বলছে, ইউনূস সরকারের সময়কার এই মৃত্যুসমূহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং বাংলাদেশের আইনি কাঠামোর জন্য “অবমাননাকর দৃষ্টান্ত”।
যদি নিরপেক্ষ তদন্ত না হয়, তবে এটি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক অঙ্গনে ‘Human Rights Blacklist’-এ ঠেলে দিতে পারে—
যার প্রভাব পড়বে বিদেশি সহায়তা, বিনিয়োগ ও আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিতে
বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রাজনৈতিক বন্দিদের মৃত্যু মানে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বলয়েই ন্যায়বিচারের মৃত্যু।
৩১টি মৃত্যুর প্রতিটি ঘটনা বাংলাদেশের গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও মানবাধিকারের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়েছে।
একটি সত্যনিষ্ঠ তদন্ত, অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনা এবং রাষ্ট্রীয় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাই পারে এই অন্ধকার অধ্যায় থেকে বাংলাদেশকে উদ্ধার করতে।
ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ধারাবাহিক মৃত্যু কেবল রাজনৈতিক ঘটনা নয়;
এটি রাষ্ট্রীয় নৈতিকতার পতন এবং আইনের শাসনের সীমাহীন দুর্বলতার প্রতিচ্ছবি।