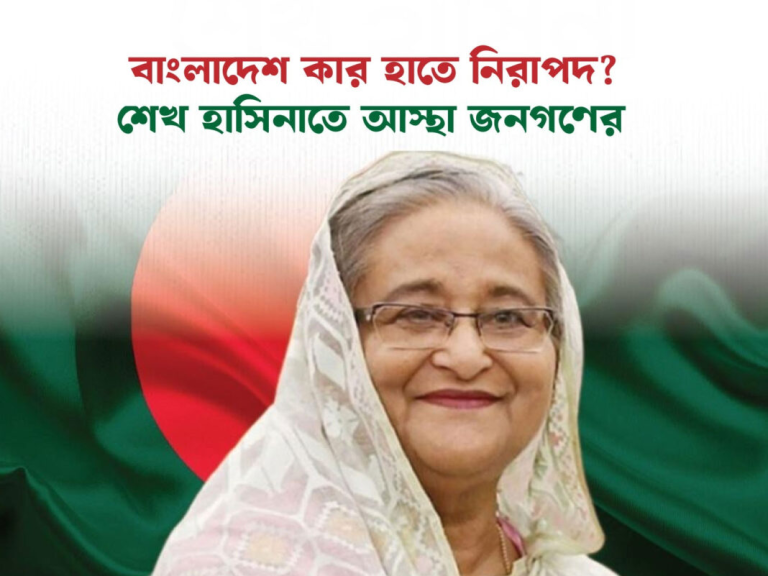নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে শ্রমিক অসন্তোষের জেরে চারটি কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা। এ সিদ্ধান্ত দেশের রপ্তানি খাত ও বিনিয়োগ পরিবেশে নতুন অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করছে।
নীলফামারীর উত্তরা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড) দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্প বিকাশের এক অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। কিন্তু হঠাৎ করেই সেখানে একসঙ্গে চারটি কারখানা — মেইগো বাংলাদেশ, ইপিএফ প্রিন্টিং লিমিটেড, সেকশন সেভেন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এবং দেশবন্ধু টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড — অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।
রোববার (২৬ অক্টোবর) বিকেলে জারি করা এই ঘোষণাটি শুধুমাত্র চারটি প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন স্থবির করে দেয়নি, বরং দেশের তৈরি পোশাক ও রপ্তানি শিল্পের সামগ্রিক স্থিতিশীলতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে।
কারখানাগুলোর নোটিশ অনুযায়ী, শ্রমিকরা শনিবার (২৫ অক্টোবর) কাজ না করে কারখানার মূল ফটকের বাইরে অবস্থান নিয়ে উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করেন।
কর্তৃপক্ষের আলোচনার আহ্বান উপেক্ষা করে পরদিনও তারা কাজে যোগ দেননি।
এর ফলে কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ ইপিজেড শ্রম আইন ২০১৯-এর ধারা ১২(১) অনুযায়ী এটি “বেআইনি ধর্মঘট” হিসেবে চিহ্নিত করে উৎপাদন বন্ধ ঘোষণা করে।
এখানে প্রশ্ন উঠছে—শ্রমিকদের দাবিগুলো কী ছিল, সেগুলো কতটা যুক্তিসঙ্গত ছিল, এবং আলোচনার সুযোগ কতটুকু দেওয়া হয়েছিল?
অতীতে ইপিজেডের মধ্যে শ্রমিক ইউনিয়ন কার্যক্রমের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকায় শ্রমিকদের অধিকারের সুরক্ষা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনা রয়েছে।
উত্তরা ইপিজেডে এই বন্ধ ঘোষণার তাৎক্ষণিক প্রভাব পড়বে স্থানীয় অর্থনীতিতে।
প্রায় কয়েক হাজার শ্রমিক এক রাতেই বেকার হয়ে পড়েছেন।
একইসঙ্গে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে বাংলাদেশের শিল্প পরিবেশ সম্পর্কে আবারও অনিশ্চয়তার বার্তা যাচ্ছে।
বর্তমানে রপ্তানি খাতের বড় একটি অংশ ইপিজেডভিত্তিক শিল্পের ওপর নির্ভরশীল।
শ্রমিক অসন্তোষ ও প্রশাসনিক অচলাবস্থা বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করতে পারে—বিশেষত যখন বিদেশি বিনিয়োগে আগের তিন প্রান্তিকে ৬০ শতাংশেরও বেশি পতন রেকর্ড হয়েছে।
মানবিক দিক ও নীতিনির্ধারকদের দায়িত্ব
কারখানা বন্ধ থাকাকালীন শ্রমিকদের বেতন, চাকরি নিরাপত্তা ও পুনর্বহালের নিশ্চয়তা নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়নি।
এতে করে হাজারো পরিবার আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়বে।
নীতিনির্ধারকদের এখন জরুরি ভিত্তিতে একটি শ্রমিক-ব্যবস্থাপক যৌথ টাস্কফোর্স গঠন করে সংলাপের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন,
যাতে উত্তরা ইপিজেডসহ দেশের অন্যান্য শিল্পাঞ্চলে এমন অনিশ্চয়তা আর না ঘটে।
ইপিজেডগুলোর সাফল্য বাংলাদেশের রপ্তানি বৃদ্ধির অন্যতম চালিকা শক্তি হলেও শ্রমিক–ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের টানাপোড়েন এখন বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
যদি এই সংকট দ্রুত সমাধান না হয়, তবে আন্তর্জাতিক ক্রেতারা বিকল্প উৎস খুঁজে নিতে পারে—যা বাংলাদেশি অর্থনীতির জন্য ভয়াবহ আঘাত হতে পারে।
উত্তরা ইপিজেডের চার কারখানার এই বন্ধ ঘোষণা কেবল একটি শ্রমিক আন্দোলনের ফল নয়;
এটি বাংলাদেশের শিল্পনীতির কাঠামোগত দুর্বলতা, শ্রমিক অধিকার ব্যবস্থাপনা এবং শিল্পাঞ্চল প্রশাসনের সমন্বয়হীনতার প্রতিফলন।
এখন প্রয়োজন, সংঘাত নয়—সংলাপ ও সুশাসনের মাধ্যমে এই সঙ্কট নিরসনের।
অন্যথায়, “রপ্তানিমুখী অর্থনীতি” হিসেবে বাংলাদেশের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।