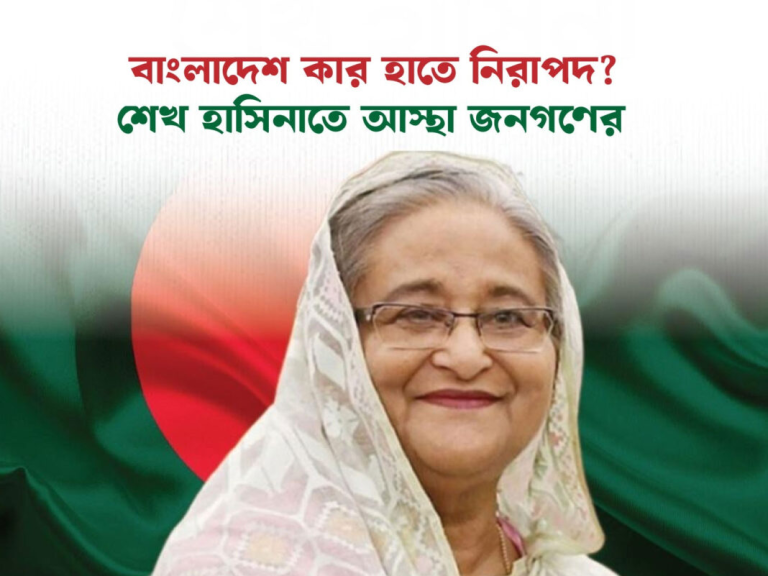চট্টগ্রামে গত এক বছরে ১১৭টি কারখানা স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়েছে। বেকার হয়েছে ৫১ হাজার শ্রমিক। এলসি জটিলতা, আর্থিক সংকট ও বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতার কারণে এ শিল্প বিপর্যয় ঘটেছে।
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পনগরী—যেখানে একসময় পোশাক, ইস্পাত ও জাহাজ ভাঙা শিল্পের গর্জন শুনে দেশের অর্থনীতির হৃদস্পন্দন টের পাওয়া যেত। কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গত এক বছরে এই শিল্পাঞ্চলে নেমে এসেছে এক ভয়াবহ মন্দা। শিল্প পুলিশের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ১১৭টি কারখানা স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে পড়েছে, ফলে বেকার হয়েছেন প্রায় ৫১ হাজার শ্রমিক।
শিল্প পুলিশের তালিকা অনুযায়ী, ৫০টি কারখানা স্থায়ীভাবে এবং ৬৭টি কারখানা অস্থায়ীভাবে বন্ধ রয়েছে।
সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পোশাক শিল্প, যেখানে গত এক বছরে ২২টি গার্মেন্টস কারখানা কার্যক্রম বন্ধ করেছে।
আর্থিক সংকট, ব্যাংক ঋণ না পাওয়া, এলসি জটিলতা, এবং বিদেশি ক্রেতাদের অর্ডার কমে যাওয়া—সব মিলিয়ে উদ্যোক্তারা পড়ে গেছেন টিকে থাকার লড়াইয়ে।
বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্যারিফ নীতির পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক বাজারে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা বাংলাদেশের পোশাক খাতকে চাপে ফেলেছে।
বিজিএমইএ পরিচালক রাকিবুল আলম চৌধুরী স্বীকার করেছেন, “স্ট্রং কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরি না হলে টিকে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়েছে।
বায়িং হাউসের মাধ্যমে যারা কাজ করতো তারা দিশেহারা।”
বন্ধ কারখানার তালিকায় রয়েছে দেশের আলোচিত দুই শিল্পগ্রুপ—আরামিট গ্রুপ ও নাসা গ্রুপ।
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী জাবেদ ও তাঁর পরিবারের মালিকানাধীন আরামিট থাই অ্যালুমিনিয়াম, আরামিট ফুটওয়্যার এবং আরামিট পাওয়ার লিমিটেড—
তিনটি প্রতিষ্ঠানই চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে।
অন্যদিকে নাসা গ্রুপের মালিকানাধীন টয় উড (বিডি) কোম্পানি লিমিটেড ও এমএনসি অ্যাপারেলস—
ইপিজেডে অবস্থিত এই দুই প্রতিষ্ঠানও ব্যাংক জটিলতা ও অর্ডার সংকটের কারণে কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছে।
শিপ ব্রেকিং শিল্পে সংকট
শুধু পোশাক নয়, চট্টগ্রামের শিপ ব্রেকিং ও ইস্পাত শিল্পেও ভয়াবহ স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।
শিল্প পুলিশের তালিকায় ১৩টি শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড ও স্টিল মিল বন্ধ হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।
বাংলাদেশ শিপ ব্রেকার্স অ্যান্ড রিসাইক্লার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি জহিরুল ইসলাম রিংকু জানান, “হংকং কনভেনশন অনুযায়ী গ্রিন শিপইয়ার্ডে রূপান্তর করতে না পারায় অনেক ইয়ার্ডের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।
ব্যাংকগুলো নতুন ঋণ দিতে পারছে না, এলসি খোলা বন্ধ।”
গত আগস্টে সীতাকুণ্ডে জাহাজ আমদানির জন্য একটিও নতুন এনওসি ইস্যু হয়নি—যা এই খাতের সংকটের গভীরতা বোঝায়।
শিল্প পুলিশের তথ্যমতে, গত এক বছরে ৭০টি কারখানায় ৩১৫টি শ্রমিক অসন্তোষের ঘটনা ঘটেছে।
সবচেয়ে সাম্প্রতিক উদাহরণ—প্যাসিফিক গ্রুপের কয়েকটি কারখানা, যা ১৪-১৫ অক্টোবর শ্রমিক আন্দোলনের কারণে অস্থায়ীভাবে বন্ধ রাখতে হয়।
এই ধরণের পুনরাবৃত্তি শুধু উৎপাদন ব্যাহত করছে না, বরং চট্টগ্রামের শ্রমবাজার ও সামাজিক স্থিতিশীলতার ওপরও সরাসরি প্রভাব ফেলছে।
বিশ্লেষকদের মতে, এই শিল্প বিপর্যয়ের মূল কারণ কেবল বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট নয়, বরং দেশের অভ্যন্তরীণ আর্থিক অনিশ্চয়তা ও রাজনৈতিক অস্থিরতাও।
ব্যাংক একীভূতকরণ, এলসি অনুমোদনে ধীরগতি, এবং সরকার পরিবর্তনের পর ব্যবসায়ীদের অনিশ্চয়তা—সব মিলিয়ে বিনিয়োগকারীরা নতুন প্রকল্পে হাত দিতে ভয় পাচ্ছেন।
অনেক উদ্যোক্তা ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন, কেউ কেউ বিদেশে বিনিয়োগ স্থানান্তর করছেন।
চট্টগ্রামের শিল্পাঞ্চল বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি।
এখানে কারখানা বন্ধ মানে শুধু শিল্প নয়, অর্থনীতি, শ্রমবাজার ও সামাজিক স্থিতি—সবকিছুর ওপর বহুমাত্রিক প্রভাব।
এই অবস্থায় দ্রুত আর্থিক নীতিগত স্থিতিশীলতা, রপ্তানি প্রণোদনা এবং ব্যাংকিং খাতের সংস্কার না হলে চট্টগ্রাম হতে পারে দেশের প্রথম বড় “ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোল্যাপ্স” জোন।