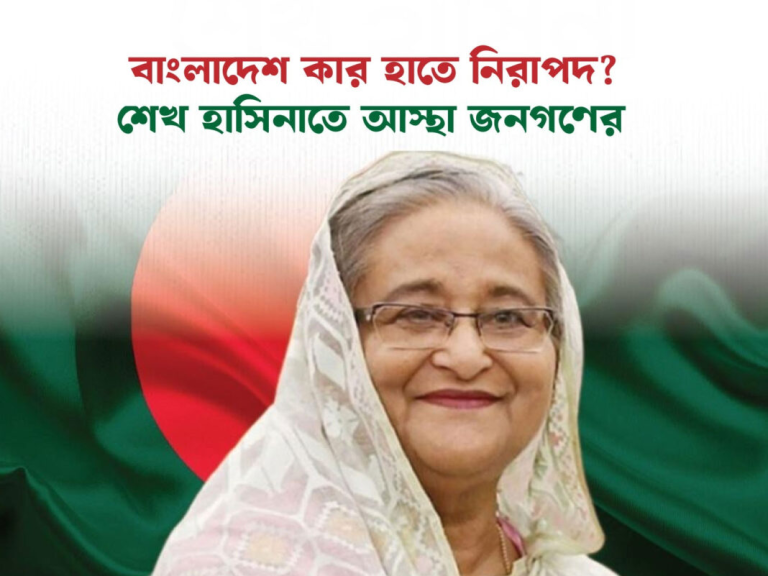২০২৪ সালে বাংলাদেশের বিক্ষোভ দমনের উপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের উপর অনৈতিক সাংবাদিকতার জন্য সজীব ওয়াজেদ জয় বিবিসির নিন্দা করেছেন, এটিকে পক্ষপাতদুষ্ট এবং বিভ্রান্তিকর বলে অভিহিত করেছেন। সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ এখানে পড়ুন।
২০২৪ সালের জুলাই-অগাস্টে বাংলাদেশে সংঘটিত ভয়াবহ ছাত্র আন্দোলন ও সেই প্রেক্ষাপটে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দমন অভিযানের ঘটনায় সম্প্রতি বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও প্রামাণ্যচিত্র প্রকাশ করেছে। সেই প্রতিবেদনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একটি কথিত ফোনালাপের উদ্ধৃতি দিয়ে দাবি করা হয়েছে, তিনি সরাসরি ‘প্রাণঘাতী অস্ত্র’ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তার ছেলে, তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়।
জয় ফেইসবুক পোস্টে বিবিসির প্রতিবেদনকে আখ্যা দিয়েছেন “অনৈতিক সাংবাদিকতার নির্লজ্জ উদাহরণ” হিসেবে।
তার বক্তব্য এবং বিবিসির তথ্যউপাত্ত—দুটোকে পাশাপাশি রেখে এই প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করলেই বেরিয়ে আসে একটি গভীর আন্তর্জাতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট।
বিবিসির দাবি, ৫ অগাস্ট ২০২৪-এ ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে পুলিশের গুলিতে অন্তত ৫২ জন নিহত হন। ফাঁস হওয়া অডিও বিশ্লেষণ করে তারা বলেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে “যেখানেই পাবে, গুলি করবে”—এমন নির্দেশ দিয়েছিলেন।
বিবিসি এই অডিওর ফরেনসিক পরীক্ষা করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Earshot-এর মাধ্যমে, যারা নিশ্চিত করেছে যে অডিওটি ‘ম্যানিপুলেট’ করা হয়নি।
প্রতিবেদনে সিসিটিভি ফুটেজ, ড্রোন ভিডিও এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য ব্যবহার করে দেখানো হয়েছে—সেনাবাহিনী সরে যাওয়ার পর পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়।
বিবিসির একপেশে তথ্য-
সজীব ওয়াজেদ জয়ের পোস্টে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো—বিবিসি একপেশে তথ্য তুলে ধরেছে, প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপট উপেক্ষা করেছে, এবং অভিযুক্তদের বক্তব্য নেওয়ার ন্যূনতম চেষ্টা পর্যন্ত করেনি।
তিনি জিজ্ঞেস করেন—
- সেনাবাহিনী কেন সরে গেল, সেই প্রশ্ন বিবিসি কেন তোলেনি?
- ড্রোন ভিডিও কে তুলেছিল, এবং আগে থেকেই ড্রোন প্রস্তুত থাকার রহস্য কী?
- কেন নিহতদের ময়নাতদন্ত হয়নি?
- যাত্রাবাড়ী থানায় পুলিশ সদস্যদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ভিডিও বিবিসি এড়িয়ে গেল কেন?
জয়ের মতে, ওইদিন দেশে কার্যকর কোনো সরকার ছিল না, এবং পুলিশ আত্মরক্ষার জন্যই গুলি চালাতে বাধ্য হয়েছিল।
বিবিসির অনুসন্ধানে ১৮ জুলাইয়ের একটি ফোনালাপকে প্রধান প্রমাণ হিসেবে হাজির করা হয়েছে। যেখানে শেখ হাসিনা ‘প্রাণঘাতী অস্ত্র’ ব্যবহারের কথা বলেন বলে দাবি করা হয়। ফরেনসিক প্রতিষ্ঠানের মতে, অডিওটি জাল নয়। তবে জয় প্রশ্ন তুলেছেন—শুধু কয়েক সেকেন্ডের একটি ক্লিপ দিয়ে প্রেক্ষাপটহীনভাবে এমন গুরুতর অভিযোগ কীভাবে তোলা যায়?
তিনি বলেন, “ফরেনসিক বিশ্লেষণও বিবিসি নিজে করেনি, অন্য প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছে। এটা কোনো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মানদণ্ডে পড়ে না।”
জয়ের বিশ্লেষণে উঠে আসে এমন কিছু দিক যা বিবিসি প্রতিবেদনে অনুপস্থিত:
- ৫ অগাস্টে পুলিশের ওপর আগাম হামলা, থানা ঘেরাও ও আগুন লাগানো ছিল একযোগে সংঘটিত একটি পূর্বপরিকল্পিত নকশা।
- কয়েকটি ভিডিওতে দেখা গেছে বিক্ষোভকারীরা দাহ্য বস্তু ও দড়ি নিয়ে প্রস্তুত অবস্থায় ছিল, যেটি আক্রমণের পূর্ব ইঙ্গিত।
- থানায় আটকা পড়ে থাকা পুলিশ কর্মকর্তারা সেনা ক্যাম্পে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন—এই বাস্তবতা বিবিসি গোপন করেছে বলে অভিযোগ জয়ের।
বিবিসি বলেছে, তারা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করেছে এবং স্বতন্ত্র ফরেনসিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তা নিয়েছে।
তবে পুরো প্রতিবেদনে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরোধী পক্ষ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিংবা পররাষ্ট্রে থাকা সাবেক শাসক দলের মুখপাত্রদের বক্তব্য অনুপস্থিত।
জয়ের মতে, এটি শুধুই তথ্য বাছাই করে সরকারি নির্যাতনকে ‘নিয়মিত প্র্যাকটিস’ হিসেবে তুলে ধরার কৌশল, যা আন্তর্জাতিকভাবে শেখ হাসিনাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা।
বিবিসির প্রতিবেদন এবং জয়-এর পাল্টা যুক্তি আমাদের সামনে আরও একবার তুলে ধরেছে আধুনিক সাংবাদিকতা কতটা রাজনৈতিক হয়ে উঠতে পারে।
এই প্রতিবেদন কি সত্যিই নিরপেক্ষ অনুসন্ধান, না কি এটি একটি আন্তর্জাতিক ন্যারেটিভ তৈরি করে শেখ হাসিনার সরকারকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা—এই প্রশ্ন এখন বাংলাদেশের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও আলোচিত।
উভয় পক্ষের তথ্যই যদি খণ্ডিত হয়, তবে সত্য কীভাবে নির্ধারিত হবে? এবং কে নির্ধারণ করবে? এই প্রশ্নের উত্তরই হয়ত ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে থাকবে।